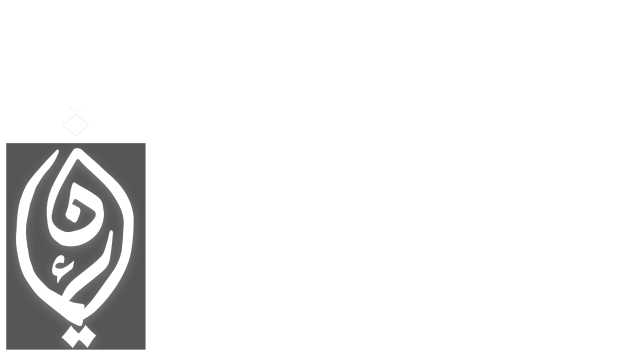লেখক: মাওলানা মুহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম
যখন মাটির নীচে একটি বীজ বপন করা হয়, তখন সে বীজ থেকে বেরিয়ে আসে সবুজ বর্ণের একটি চারা, তা থেকে হয় কান্ড, কান্ড থেকে ধীরে ধীরে গজিয়ে উঠে ডালপালা। ঠিক তেমনিভাবে যে কোন উসূল বা মূলনীতি থেকে নির্গত হয়ে আসে অনেক শাখা প্রশাখা। শরীয়তের মাস্আলা-মাসায়েরে ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম ঘটে নি। আসল বা মূলকে কেন্দ্র করে ফরা’ – ফুরুয়াত তথা শাখা প্রশাখা নির্গত করার এই অসংখ্য ধারার মানবজীবনের – সকল পর্ব, সকল শাখা প্রশাখা ও দিক দিগন্তকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে শরীয়ত। শরীয়তেরই অপর নাম জীবনধর্ম, জীবনবিধান। জীবনযাত্রার প্রতিটি ক্ষেত্রে – জন্ম থেমে মৃত্যু পর্যন্ত একজন মুসলমান উক্ত বিধানকে মেনে চলতে হয়। মেনে চলতে হয় শরীয়তের দিকনির্দেশনা । তথা মাসআলা-মাসায়েলের বাহিরে মুসলিম জীবনের নেই কোন পর্ব। অপরদিকে মানব জীবনের সমস্যা ও অন্তহীন এবং নিত্য নতুন। প্রতিদিন সম্মুখীন হতে হয় বিচিত্র সব জিজ্ঞাসার। আল্লাহতে আত্মসমর্পিত মুমিন বান্দাদেরকে তো আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের আলোকে এর জবাব দিহে হবে। আর উদ্ভাবিত যে কোন প্রশ্ন-সমস্যার ফয়সালা-সমাধান ইসলামের মূলনীতির ভিত্তিতে দিতে হবে। সে জন্যই প্রয়োজন হয় মাসআলার, সে জন্যই জরুরী-দরকারী হয়ে ওঠে শরয়ী দিকনির্দেশনার। আর এই প্রেক্ষিতেই অত্যাবশ্যকীয় হয়ে ওঠে ফতোয়া। ফতোয়া ইসলামের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। ফতোয়া ছাড়া ইসলামী জিন্দেগী অচল। ইসলামী জীবনগঠনে ফতোয়া অবশ্যই জরুরী। আর যেহেতু প্রত্যেক মহৎ কাজ আঞ্জাম দিবেন একমাত্র ঐ সকল ব্যক্তিত্ব – যারা ইসলামিক পন্ডিত ও ইসলামী আইন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অবহিত, যাদেরকে আমরা মুফতী বা ফক্বীহ বলে থাকি। এদের ব্যতীত অন্য কেউ যদি ফতোয়া প্রদান করে যেমন – গ্রাম্য বা স্থানীয় নেতা, এমনকি ইসলামী আইন সম্পর্কে ব্যাপকভাবে অবহিত নন এমন সূধীদের ফতোয়া, তাহলে তা হবে ফতোয়ার অপব্যবহার। তাই ফতোয়ার অপব্যবহারকে রোধ করা মুসলমানদের জন্য অত্যাবশ্যকীয়। আর এটাকে সঠিকভাবে রোধ করতে হলে কালক্রমে প্রচার মাধ্যমের ঐকান্ডিক প্রচেষ্টার দ্বারা জনগণকে অবহিত করতে পারলেই কেবল সম্ভব।
সুতরাং আমাদেরকে ফতোয়া, তার গুরুত্ব এবং অপব্যবহার ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। এর সাথে সাথে ফতোয়ার অপব্যবহার থেকে নিজেকে বিরত রাখতে হবে এবং অন্যকেও বিরত রাখতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদেরকে তৌফীক দান করুন। আমীন।
ফতোয়ার বিশ্লেষণ
ফতোয়া ইসলামের একটি অতি পবিত্র, ভাব গাম্ভীর্য ও মর্যাদাপূর্ণ শব্দ।
ফতোয়া শব্দের মূল ধাতু ফা, তা, ইয়া। এ বর্ণত্রয়ের সমন্বিতরূপ ”ফাতয়ুন” থেকে নির্গত। কিন্তু উচ্চারণের সুবিধার্থে উক্ত “ইয়া” অক্ষরটিকে “ওয়াউ” দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। তার অর্থ হচ্ছে – ফয়ছালা, সমাধান, মুফতীর নিস্পত্তি, কাজীর রায়, ইত্যাদি।
“আল-মুগরিব” নামক গ্রন্থে আছে যে, ফতোয়া শব্দটি “ফুতা বা ফাতা” থেকে নির্গত। এর অর্থ – অস্পষ্ট কথা, এবং ইফতা অর্থ উক্ত অস্পষ্টতাকে দূর করে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা।
সুপ্রসিদ্ধ আরবী অভিধান “আল-ক্বামূছ” এর রচয়িতা আজ থেকে প্রায় পাঁচশত বছর পূর্বে নিজ যুগে নিজ দেশে প্রধান বিচারপতি ছিলেন। তিনি ফতোয়া শব্দটির অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন: .. অর্থাৎ ফিক্বাহবিদগণ যা সমাধান প্রদান করেন তা-ই ফতোয়া।
“আল-মুনজিদ” অভিধানগ্রন্থে লিখা আছে যে, ফতোয়া হচ্ছে শরীয়ত বিশেষজ্ঞ ব্যাক্তির শরীয়ত সংক্রান্ত ফায়সালা।
“আল-ক্বামূছুল ফিক্বহী” নামক গ্রন্থে বর্ণিত যে, শরয়ী বিধি-বিধান দ্বারা মানবিক সমস্যাবলীর সমাধানই হলো ফতোয়া।
আল্লামা ইবনুল মানযূর ইফরীক্বী (রাহ:) “লিসানুল আরব” গ্রন্থে বলেন: ফতোয়া অর্থ হচ্ছে – উদ্ভাবিত যে কোন প্রশ্নের সমাধান দেয়া। আর এটাই অধিক শুদ্ধ ও সহীহ।
শরীয়তের পরিভাষায় ফতোয়া
লুগাত বা আভিধানিক অর্থে যদিও ফতোয়া শব্দটি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে এক বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হতে লাগলো। অর্থাৎ শরীয়ত সম্পর্কিত যে কোন প্রশ্নের জবাব বা সমাধান দেয়াকে ফতোয়া বলা হয়। এ মর্মে ফতোয়া শব্দটি ক্বোরআন-হাদীসে বহুল ব্যবহৃত। যেমন: .. অর্থাৎ বলুন হে রাসূল (সা:) আল্লাহ তোমাদের ফতোয়া দিচ্ছেন কালালার মিরাছ সংক্রান্ত বিষয়ে। (সূরায়ে নিসা, আয়াত নং ১০৬) (মা’আরিফ: ৩০২)
অন্যত্র আল্লাহ তায়ালা বলেন: .. অর্থাৎ হে নবী লোকেরা যদি আপনার নিকট নারীদের বিষয়ে ফতোয়া চায়, আপনি তাদেরকে বলে দিন, আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের সম্বন্ধে ফতোয়া দিচ্ছেন। (সূরায়ে নিসা: ১২৭)
ফতোয়া শব্দটি হাদীসেও অনুরূপ ব্যবহৃত। যেমন: .. অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে যে ফতোয়া দেয়ার ক্ষেত্রে যত সাহসী, দুযখের পথেও সে তত সাহসী।
অন্য হাদীসে আছে: ..অর্থাৎ
উপরোল্লেখিত সংজ্ঞাকে এভাবে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে যে, যেহেতু ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান, তাই দৈনন্দিন জীবনে ইসলামী অনুশাসন সম্পর্কে জ্ঞাত হওয়ার উদ্দেশ্যে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে ইসলামী আইন বিশারদগণ বা ফক্বীহগণ যে বিজ্ঞ মতামত প্রদান করেন, তা-কেই সাধারণ অর্থে ফতোয়া বলা হয়।
অথবা এভাবেও বলা যেতে পারে যে, মানুষ দৈনন্দিন জীবনে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিকসহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধান চেয়ে দেশের আস্থাভাজন ওলামায়ে কেরামের দ্বারস্থ হয়ে ইসলামের মূলনীতি (কুরআন, হাদীস, ইজমা, ক্বিয়াস) অনুযায়ী যে সিদ্ধান্তকারী অভিমত ও বিচারকের ফায়সালা পেয়ে থাকেন তা-কেই ফতোয়া বলা হয়।
ফতোয়া শব্দ ছাড়া আরও কয়েকটি শব্দ আরবী অভিধান গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়। যেমন: ফুতইয়া, ইফতা, ইস্তেফতা। এ শব্দত্রয়ের সম্পর্কে এখানে কিঞ্চৎ আলোচনা করে নেয়া উচিত।
“ফুতইয়া” নতুন কোন শব্দ নয়। বরং এ থেকেই ফতোয়া শব্দটি নির্গত। উচ্চারণের সুবিধার্থে ‘ইয়া’কে “ওয়াউ” দ্বারা পরিবর্তন করা হয়। উক্ত শব্দে “ফা” অক্ষরে যবর হবে না পেশ হবে? এ ব্যাপারে অভিধানে উভয় ব্যবহার পাওয়া যায়, তবে যবর হওয়াই অথিক সহীহ ও শুদ্ধ। যেমন “মিছবাহুল মুনীর” নামক অভিধানে উল্লেখ আছে। এর বহুবচন “..” মতান্তরে “..”।
“ইফতা ও ইস্তেফতা” এ শব্দদ্বয়ও পৃথক কোন শব্দ নয়। .. এর ভিন্নতার দরুণ অর্থে ব্যবধান হয়ে যায়। যেমন- ইস্তেফতা অর্থ চাওয়া, ফতোয়ার জন্য প্রশ্ন করা। আর ইফতা শব্দ কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত। যেমন “বর্ণনা করা”। কোন বিষয় বর্ণনা করা হলে বলা হয়: .. অথবা যখন কোন ব্যক্তির প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়, তখন বলা হয়: .. অথবা স্বপ্নের তা’বীরের জন্য প্রশ্ন করা হলে তা’বীর করাকে ইফতা বলা হয়। যেমন..
মোটকথা অভিধান গ্রন্থাবলী তথ্য-তালাশের পর এ কথাই বুঝা যায় যে, ইফতা শব্দটি তখনই ব্যবহার হয় যখন কোন প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়।
ইবনুল মানযূও ইফরীক্বী (রহ:) “লিসানুল আরব” এ বলেন যে- ফতোয়া, ফুতইয়া, ইফতা এ শব্দত্রয় একই অর্থে ব্যবহৃত হয়।
ইফতা শব্দে কয়েকটি মনোমুগ্ধকর কৌতুক
১) ইফতা শব্দটি ব্যবহারের দু’টি দিক রয়েছে। একটি হল, এটা .. থেকে .. এর একটি অপরিবর্তনশীল ক্রিয়া। অপরদিকে এটা .. থেকে ..্ এর একটি পরিবর্তনশীল ক্রিয়া।
প্রথম দিক হিসেবে কৌতুক: যেভাবে উক্ত শব্দটি অপরিবর্তনশীল, অনুরূপ মুফতীর জন্য উচিৎ হল, তিনি যেন ফতোয়া প্রদানে শরীয়তের অকাট্য হুকুম-আহকাম ও মূলনীতির মধ্যে কোন প্রকারের পরিবর্তন না আসতে দেন
দ্বিতীয় দিক হতে কৌতুক: যেহেতু শব্দটি পরিবর্তনশীল, তাই মুফতীর জন্যও শরীয়তের অকাট্য, প্রাসঙ্গিক হুকুম-আহকাম এবং নিজ প্রচেষ্টায় উদ্ভাবকৃত মাসআলা-মাসায়েল পরিবর্তন করা জায়েয।
২) ইফতা শব্দটি .. এর সংক্রামক (..) ক্রিয়া। তাই মুফতী ঐ ব্যক্তিই হবেন যার ইলম ও সংক্রামক হয়, এবং তা থেকে সর্বদা আশরাফুল মাখলুক্বাত উপকৃত হয়।
৩) ইফতা শব্দটি যেহেতু .. এর একটি মাছদার বা উৎস। সুতরাং আশা করা যায় যে, আল্লাহ তায়ালা মুফতী সাহেবকে শরীয়তের হুকুম-আহকাম ও নিত্য-নতুন আবিষ্কৃত মাসআলা-মাসায়েল এবং সু² বিষয়াদিও ফতোয়া প্রদানে .. অর্থাৎ অতিরিক্ত যোগ্যতা ও জ্ঞানের ভান্ডার খোলে দেবেন।
৪) ইফতা শব্দের প্রথম এবং শেষ অক্ষর হলো “হামযা”। তাই এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয় এ দিকে যে, মুফতী সাহেব ফতোয়া প্রদানে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অটল থাকা জরুরী। এ কথাও বুঝা যায় যে, তিনি সত্যবাদি ও আমানতদার থাকতে হবে।
৫) ইফতা শব্দের প্রথমে যে হামযা এটা ক্বাতয়ী। এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয় এ দিকে যে, মুফতীর জন্য সর্ব প্রথম জরুরী ও অপরিহার্য কাজ হলো “..” অর্থাৎ লোভ, লালসাকে ত্যাগ করা, এবং ফতোয়া দেয়াকে ইসলামের খেদমত মনে করা। এবং এর বদলা পরকালে খোদা তায়ালার কাছ থেকে পাওয়ার আশা রাখা।
৬) ইফতা শব্দ থেকে এ কথাও বুঝা যায় যে, ফতোয়া প্রদানকারী যুবক ও শক্তিশালী হতে হবে। বৃদ্ধ হলে হবে না। কেননা মুফতী সাহেবের সামনে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রকারের প্রশ্নাবলী পেশ হয়। মুফতী সাহেবের জন্য এ গুলো সহ্য করা উচিৎ। কিন্তু যদি বৃদ্ধ হল, তাহলে সহ্য করা সম্ভব নয়। কারণ ধৈর্য শক্তি লোপ পাওয়ায় তিক্ততা ও বিরক্তিবোধ করবেন।
৭) ইফতা শব্দের সংখ্যাগত মান ৪৮২। এর দ্বারা ইঙ্গিত হয় এ দিকে যে, মুফতী সাহেব এর নিকট উসূল ও ফুরু’ তথা মূল বিষয় ও আনুসাঙ্গিক বিষয়ের উপর কমপক্ষে ৪৮২ টি কিতাব থাকা প্রয়োজন। এর চেয়ে কম উচিৎ নয়। (আল মিছবাহ: ১/১৭-১৮)
প্রাসঙ্গিক আলোচনা: “মুস্তাফতী বা ফতোয়াপ্রার্থীদের জন্য কিছু নিয়মনীতি”
শরীয়তের বিধি-বিধান, আইন-কানুন জানা না থাকলে একজন মুসলমান হিসেবে শরীয়ত বিশেষজ্ঞদেও নিকট থেকে জেনে নেয়া তার ঈমানী দায়িত্ব ও কর্তব্য। তবে মুফতীর কাছ থেকে ফতোয়া নেয়ার পূর্বে অবশ্যই কিছু নীতিমালার প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।
যেমন: ফতোয়াপ্রার্থী পরহেজগার ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে।
অহেতুক তর্ক, বাক-বিতন্ডায় লিপ্ত হওয়ার জন্য মুফতীর কাছে ফতোয়া চাওয়া মোটেই ঠিক নয়। এটা থেকে বিরত থাকতে হবে।
জনগণের সামনে মুফতী বা একজন আলিমকে হেয় প্রতিপন্ন করার অসৎ উদ্দেশ্যে ফতোয়া চাওয়া নিষেধ। সুতরাং অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে ফতোয়া চাওয়া যাবে না বরং ব্যবহারিক জীবনে যে বিষয়ে শরীয়ত-এর বিধান জানার বাস্তব প্রয়োজন দেখা দেয়, সে বিষয়ে অবশ্যই ফতোয়া চাওয়া যাবে।
ইসলাম সর্বক্ষেত্রেই সকলের অধিকার যথাযথ সংরক্ষণ করে এবং অনাধিকার চর্চাকে কঠোর হস্তে প্রতিরোধ করে। ফতোয়া প্রদানের অধিকারও ইসলাম নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। সাহাবায়ে কেরামের যুগে বিশেষভাবে নির্বাচিত কতিপয় সাহাবীই ফতোয়া প্রদান করতেন। মুসলিম শাসনামলে সরকার স্বীকৃত ওলামায়ে কেরামের সমন্বয়ে গঠিত “ফতোয়া বোর্ড” থেকে ফতোয়া প্রদান করা হত। খতীবে বাগদাদী (রাহ:) “আল ফিক্বহু ওয়াল মুতাফাক্কিহ” নামক গ্রন্থে লিখেন, “সরকারের কর্তব্য হলো মুফতী নিয়োগের ক্ষেত্রে উত্তমরূপে যাচাই-বাছাই করা। দেশের শীর্ষস্থানীয় ওলামায়ে কেরামের সত্যায়ন ও অনুমোদনে যারা ফতোয়া প্রদানের যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, সরকার তাদেরকে এ পদে নিয়োগ করবেন। অযোগ্যদের প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারি করবেন। কেউ নিষেধাজ্ঞা লঙ্ঘন করলে কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করবেন।”
ফতোয়া প্রদানকারী তথা মুফতী হওয়ার পূর্বশর্তাবলী
ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রাহ:) পরিষ্কার ভাষায় বলেন: “পবিত্র কুরআন সুন্নাহর ভ্যুৎপত্তি সম্পন্ন জ্ঞানী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো জন্য ফতোয়া দেয়া বৈধ নয়”।
ইমাম নববী (রাহ:) “শরহুল মুহায্যাব” গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেন, ফতোয়া প্রদানকারী বা মুফতীর মধ্যে নি¤েœাক্ত শর্তাবলী থাকা অপরিহার্য। শর্তগুলো নিম্ন রূপ:
(১) সর্বপ্রথম একজন মুফতীকে প্রকৃত মুসলমান হতে হবে। (২) মুকাল্লাফ বিশ্শরা’ বা শরীয়তের পূর্ণ অনুসারী হতে হবে। (৩) সবার দৃষ্টিতে তিনি একজন বিশ্বস্থ ব্যক্তি হতে হবে। (৪) যে সমস্ত কর্মের কারণে শরীয়তের দৃষ্টিতে লোকজন ফাসিক বলে বিবেচিত হয়, তা হতে সম্পূর্ণ বিরত থাকতে হবে। (৫) ন্যায়পরায়ণ হওয়ার সাথে সাথে সকল শ্রেণীর মানুষের জন্য উদারমনা হতে হবে। (৬) ফক্বীহুন্ নফস ও মুত্তাক্বী-পরহেজগার হতে হবে। (৭) সৎচিন্তাশীল, সূ²দর্শী, তী² মেধার অধিকারী হতে হবে। (৮) মাসআলা ইস্তেম্বাত করার যোগ্যতা থাকতে হবে। (৯) মুফতী যে ইমামের অনুসারী হবেন, তাকে সে ইমামের মাসায়েল, উসূল ও ক্বাওয়াইদ এবং সর্বক্ষেত্রে ইমামের নিয়ম-পদ্ধতির অনুসরণ করেই ফতোয়া দিতে হবে। (১০) কুরআন-হাদীসের নাছিখ-মানছূখ, মুহকাম-মুতাশাবেহ ইত্যাদির ইলম থাকতে হবে। (১১) স্বীয় যামানার হাল-অবস্থা এবং নিয়ম-নীতি সম্পর্কে ও জ্ঞান থাকতে হবে। (১২) কোন যোগ্য মুফতীর নিকট থেকে ফতোয়া দেয়া এবং তৎসংশ্লিষ্ট আইন-কানুন ও নিয়ম-নীতির বিশেষ প্রশিক্ষণ নিতে হবে। অনেকে এ শর্তটিকে মুফতির জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ বলে আখ্যা দিয়েছেন। (১৩) সর্বপ্রকার মনেবৃত্তি এবং নাজায়েয হিলা-বাহানা থেকেও পূর্ণরূপে বিরত থাকতে হবে। (১৪) খোলাফায়ে রাশিদীন ও সাহাবায়ে কেরামের কর্মনীতি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকতে হবে। (১৫) অতীতের মুজতাহিদ ওলামা ও ফক্বীহগণের মতামত সম্পর্কে অবহিত থাকতে হবে। (১৬) নি:স্বার্থভাবে আল্লাহভীতির সাথে হক্ব কথা বলতে হবে। (১৭) যে মাসআলা সম্পর্কে ফতোয়া দেবেন, এর উপর নিজেরও আমল থাকতে হবে। যাতে করে কথা ও কাজ-এর মধ্যে বিরুধ সৃষ্টি না হয়।
উপরোল্লেখিত শর্তাবলী একজন মুফতীর জন্য অত্যাবশ্যকীয়। কোন একটি না পাওয়া গেলে তার জন্য ফতোয়া প্রদান করা জায়েয নয়।
ফতোয়া প্রদানের হুকুম
ইলমে ফিকহের কিতাবাদিতে লিখা আছে যে, ফতোয়া প্রদান করা ফরযে কিফায়াহ। প্রতিটি মুসলমানকে যেহেতু ইসলামী শরীয়ার প্রতিটি বিধান বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলতে হয়, তাই শরীয়তের জ্ঞান অর্জন প্রতিটি মুসলমানের উপর অপরিহার্য হয়ে পড়ে। আর এ কারণেই প্রত্যেকের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার সাথে সংশ্লিষ্ট ইলম যাকে “ইলমে হাল” বলা হয়, যা অর্জন করা ফরযে আইন তথা সার্বজনীন ফরয। কিন্তু জীবন পথে চলতে নতুন অনেক ঘটনার অবতারণা ঘটে। সাধারণ ইলম দ্বারা সে সবের সুরাহা হয় না। সাধারণ ইলমে ফিকহের কিতাবাদিতেও সমাধান খুঁজে পাওয়া যায় না। বরং এগুলোর মীমাংসার জন্য ইলমে ফিকহের সুগভীর ইলমের প্রয়োজন হয়। শরয়ী বিধানাবলীর ব্যবহার ব্যবহার-বিধি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান প্রত্যেকের জন্য রীতিমত অর্জন করা কঠিন, তাই এ শ্রেণীর ইলমকে সার্বজনীন আবশ্যক করা হলে অনেকেই স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বিপন্ন হবে বিধায় পরম দয়াময় আল্লাহ তায়ালা এলাকাভিত্তিক নিম্নে একজন-এর উপর এ ইলম অর্জন করা ফরয করে দেন। এলাকার কেউ যদি তা অর্জন না করেন, তাহলে সকলই গোনাহগার হবে। এ শ্রেণীর ইলম অর্জনকারীদেরকেই ফক্বীহ বা মুফতী বলা হয়।
আদাবে ফতোয়া বা ফতোয়ার আদবসমূহ
ফতোয়া প্রদানের (লিখিতভাবে হোক বা মৌখিকভাবে হোক) অনেক আদাব রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি নিম্নে বর্ণিত:
১) ফতোয়া প্রদানে সর্তকতা অবলম্বন করা: অর্থাৎ ফতোয়া লিপিবদ্ধ বা ফতোয়া দেয়া অতি মর্যাদাপূর্ণ ও পূণ্যের কাজ হওয়ার সাথে সাথে নিজের মধ্যে মাধুর্যতাও রাখে। কারণ মুফতী সাহেবের পদমর্যাদা আল্লাহ ও তার বান্দাদের মধ্যে মধ্যস্থতার। যদি তিনি সঠিক মাসআলা বর্ণনা করে দেন তাহলে নিজের কর্তব্য আদায় করে পূণ্যের দাবীদার হয়ে গেলেন। আর যদি (আল্লাহ না করুক) ভূল মাসআলা বর্ণনা করেন, এবং মুস্তাফতী বা ফতোয়াপ্রার্থী এর উপর আমল করে নেয়, তাহলে এর ভূক্তভোগী মুফতী সাহেবকেই হতে হবে। এ জন্য ফতোয়া প্রদানে সাবধানতা অবলম্বন করা জরুরী। মাসআলা সম্পর্কে পূর্ণ জ্ঞাত না হওয়া পর্যন্ত ফতোয়া প্রদান করা জায়েয নয়। এতা নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করাকে দোষনীয় মনে করা ঠিক নয়। যেমন: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও ইবনে আব্বাস (রাযি:) থেকে বর্ণিত, তাঁরা বলেন: … অর্থাৎ যে ব্যক্তি সকল জিজ্ঞাসার জবাব দেয়াকে জরুরী মনে করে সে পাগল। ইমাম মালিক (রাহ:) সম্বন্ধে বলা হয় যে, তাঁকে এক মজলিসে ৪৮ টি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হলে তিনি ৩০ টি সম্পর্কে নির্দ্বিধায় .. আমি জানি না বলে উত্তর দেন। আবার কখনও তাঁর নিকট এক সাথে ৫০ টি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়, কিন্তু তিনি একটি প্রশ্নেরও জবাব দেন নি। এবং বলেন যখন কোন ব্যক্তির নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করা হয়, তখন উত্তর দেয়ার আগে তার জন্য উচিত হল, সে যেন বেহেস্ত ও দোযখকে তার অন্তর্দৃষ্টির সম্মুখে রেখে এ কথা চিন্তা করে যে, আমি কীভাবে দোযখ থেকে মুক্তি পাব। এর পর যেন উত্তর দেয়।
২) প্রশ্ন ভালভাবে পড়া: অর্থাৎ যখন মুফতী সাহেবের সামনে প্রশ্ন পেশ করা হবে, তখন মুফতী সাহেব খুব চিন্তা-ফিকর ও একাগ্রতার সাথে প্রশ্নটি পড়ে প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য ভালভাবে বুঝার প্রচেষ্টা করবেন। প্রশ্নে কোন অস্পষ্টতা থাকলে প্রথমে প্রশ্নকারীর কাছ থেকে এর বিশ্লেষণ জানবেন। অনুরূপ যদি লিখার মধ্যে কোন মারাত্মক ভূল থাকে তাহলে তা শুদ্ধ করে দিবেন। অতপর জবাব প্রদান করবেন।
৩) প্রশ্নে মধ্যখানে বা শেষে যদি শূন্যস্থান থাকে তাহলে মুফতী সাহেবের করণীয়: যদি প্রশ্ন এমনভাবে লিখা হয় যে, প্রতি দু’লাইনের মধ্যখানে বা প্রশ্নের শেষে এমন পরিমাণে শূণ্যস্থান থাকে যেখানে পরবর্তীতে প্রশ্ন বাড়ানোর বা সংযুক্ত করার আশঙ্কা থাকে, তাহলে মুফতী সাহেবের জন্য উচিৎ হল ঐ শূন্যস্থানগুলো পূর্ণ করে দেয়া। যাতে করে ভবিষ্যতে কোন ফিৎনায় পতিত না হন।
৪) ফিৎনার আশঙ্কা হলে মৌখিকভাবে জবাব দেয়াই যথেষ্ট: অর্থাৎ যদি মুফতী সাহেব কোন সন্ধানে জ্ঞাত হয়ে যান যে, প্রশ্নের জবাব প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্যের বিপরীত হবে, এবং সে কখনও ফতোয়া মানবে না; অথবা জবাব লিখে দেয়া ফিৎনার কারণ হয়ে যাবে; তখন জবাব না লিখে প্রশ্নকারীকে শুধু মৌখিক জবাব দেয়াই ভাল।
৫) যখন কয়েকটি ইস্তেফতা বা প্রশ্ন একত্রিত হবে, তখন কোন প্রশ্নের জবাব প্রথমে দিবেন? এ ব্যাপারে নিয়ম হল যে, মুফতী সাহেব ঐ প্রশ্নের জবাব প্রথমে দিবেন যেটি তাঁর নিকট প্রথমে এসেছিল। অতপর দ্বিতীয়টির, অর্থাৎ শৃঙ্খলাভাবে জবাব দিবেন। তবে যদি কোন মুসাফির বা মহিলা অথবা এমন কোন ব্যক্তির প্রশ্ন হয়, যার জবাব দিতে বিলম্ব হলে তার ক্ষতির আশঙ্কা বোধ হয়। তখন আর শৃঙ্খলাভাবে দেয়া জরুরী নয়, বরং এদের জবাব আগে দেয়াই উত্তম। যদিও তাদের প্রশ্ন শেষে পেশ করা হয়।
৬) ফতোয়া প্রদানে (বিশেষত লিখার সময়) সময় নিম্নোক্ত কাজগুলো করা: (ক) ফতোয়া লিখার শুরুতে “আউযু বিল্লাহ” “বিসমিল্লাহ”, দরূদ শরীফ, লা হাউলা –আযীম পর্যন্ত এবং “..” পাঠ করা উচিৎ। (খ) কাগজের ডান দিক থেকে ফতোয়া লিখা আরম্ভ করা। (গ) সর্বপ্রথম “..” বা .. লিখা। (ঘ) বিসমিল্লাহর পর “..” বা .. অথবা এ মর্মের কোন শব্দ লিখা। উভয়টা একত্রিত করে নিলে “..” জ্যোতির উপর জ্যোতি। (ঙ) জবাব লিখার পর “..” বা অনুরূপ বা শব্দ লিখা। (চ) অতপর নিজের দস্তখত দেয়া। (ছ) দস্তখতের নীচে তারিখ উল্লেখ করা।
৭) নিশ্চিত জবাব দেয়া: অর্থাৎ সাধারণ লোকদের প্রশ্নের জবাবে উলামায়ে কেরামের মতানৈক্য, বা পরস্পর-বিরুধী হাদীস না লিখে নিশ্চিত জবাব দেয়া উচিৎ। যাতে করে মুস্তাফতী নিশ্চিন্ত হয়ে একাগ্রচিত্তে এ উপর আমল করতে পারে। আর যদি নিশ্চিত সমাধান জানা না থাকে, তাহলে এ ব্যাপারে হয়ত নিরবতা পালন করবেন, না হয় অন্য কোন বড় মুফতী সাহেবের নিকট যাওয়ার পরামর্শ দিবেন। তবে যদি কোন বিশেষ ব্যক্তিত্ব যেমন, “আলিম উলামা” ভালরূপে মাসআলা বুঝার উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে থাকেন, তাহলে বিস্তারিত জবাব দিলেও অসুবিধা নেই।
৮) প্রদানকৃত ফতোয়া বা জবাবের বর্ণনা সুস্পষ্ট, মিষ্টভাষী এবং শুদ্ধ হওয়া উচিত। যাতে লোকদের সহজেই বোধগম্য হয়।
৯) প্রশ্নের জবাব মধ্যবর্তী আকারে লিখা। অর্থাৎ একেবারে বারিকও নয়, আবার মোটাও নয়। তদ্রƒপ একই ফতোয়ায় বিভিন্ন ধরণের লিখা, বিভিন্ন কালির কলম ব্যবহার করা ঠিক নয়।
১০) পারতপক্ষে জবাব লম্বা করে লিখা উচিৎ নয়। সংক্ষেপ হওয়া বাঞ্চনীয়। তবে মুস্তাফতী বা ফতোয়াপ্রার্থীর যদি বুঝতে অসুবিধা হয়, তাহলে লম্বা করে লিখায় অসুবিধা নেই।
কাজী আবূ হামিদ (রাহ:) থেকে বর্ণিত যে, তাঁর নিকট একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করা হল, যার শেষে এ শব্দটি ছিল: .. । তখন তিনি উত্তরে শুধু .. বলেই নিরব থাকেন।
১১) যদি মুফতী সাহেবের নিকট কেউ কোন মাসআলা নিয়ে আসে, কিন্তু তার উদ্দেশ্য শরীয়তের হুকুম জানা নয়, বরং মুফতী সাহেবকে অযথা প্রশ্ন করা বা পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য হয়, আর মুফতী সাহেব তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে কোন মাধ্যমে জ্ঞাত হয়ে যান; তাহলে এমন ব্যক্তির প্রশ্নের জবাব না দেয়াই শ্রেয়। কেননা এর দ্বারা দ্বীনের কোন উপকার হওয়ার আশা নেই ।
১২) যখন মন চিন্তান্বিত থাকে, স্বভাবজাত প্রশান্তি না থাকে, কষ্টকর অবস্থায় থাকেন, যেমন ক্রোধ, ক্ষুধা, পিপাশা, অতিগরম ইত্যাদি অবস্থায় ফতোয়া প্রদান না করাই উত্তম। কেননা ঐ সমস্ত অবস্থায় ভুলের অধিক সম্ভাবনা রয়েছে।
১৩) যদি মুস্তাফতী নিজে এসে তার প্রশ্ন পেশ করে। আর মাসআলা এমন হয় যে, এত চিন্তা-ফিকর করার প্রয়োজন হয়, তাহলে উচিৎ হল তাকে অন্য সময় আসার কথা বলে দেয়া। কারণ তাড়াহুড়ার মাধ্যমে জবাব লিখায় সাধারণত ভুল হয়ে থাকে। এবং দ্বিতীয় বার এ ভুল শুদ্ধ করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।
১৪) ফতোয়া আদবসমূহের মধ্যে এটিও একটি যে, যদি প্রশ্ন লিখিত কাগজে পূর্ণরূপে জবাব লিখা সম্ভব না হয়, তবুও প্রশ্নের পরবর্তী শূণ্যস্থান থেকে জবাব লিখা। অতপর অপর পৃষ্ঠা খালি থাকলে সেখানেও লিখা। অপর পৃষ্ঠা পূর্ণ করার পর নতুন কাগজ ব্যবহার করা। কিন্তু প্রথমেই নতুন কাগজ ব্যবহার করে নেয়া আদাবের বিপরীত কাজ।
১৫) প্রমাণপঞ্জি বা তধ্যসূত্র লিখার আদাব: (ক) যে কিতাবের নাম তথ্যসূত্র হিসেবে উল্লেখ করা হবে, এর পৃষ্ঠা, এবং কিতাব কয়েক খন্ড হলে এরও নাম্বার ও মুদ্রণালয়সহ লিখা। (খ) যদি কিতাবের বিভিন্ন নুসখা হয় তাহলে পৃষ্ঠা, খন্ড, মুদ্রণালয় উল্লেখ করার সাথে সাথে পরিচ্ছেদ (বাব, ফছল) ও উল্লেখ করা উত্তম। (গ) মাসআলাটি মূল কিতাবে না দেখা পর্যন্ত অন্য কোন রচিত কিতাবের প্রমাণ পেশ না করা। হ্যাঁ, যদি মূল গ্রন্থ না পাওয়া যায়, তাহলে যে গ্রন্থের হাওয়ালা বা তথ্য পেশ করবেন, ঐ গ্রন্থের নামও উল্লেখ করবেন।
১৬) প্রদানকৃত ফতোয়াটি নিজের খাতা বা ডায়রীতে লিখে হেফাজতে রাখা। কেননা এটা বিভিন্ন ফিৎনা থেকে বাচার মাধ্যম।
১৭) মহিলা বা ছোট বাচ্চার হাত থেকে ইস্তেফতা মুফতী সাহেব নিজে না নিয়ে ছাত্র বা অন্য কারো মাধ্যমে সংগ্রহ করে জবাব লিখা। অতপর উক্ত মাধ্যমে জবাব পৌঁছানো। এটাই ছিল অনেক উলামায়ে কেরামের আমল। এতে ইলমের সম্মান প্রদর্শন হয়। বর্তমানে এ ফিৎনার যুগে মুফতী সাহেবদের জন্য অনুরূপ করাই সতর্কতা।
১৮) যদি রাস্তায় চলাকালীন কেউ প্রশ্ন করে, তাহলে তৎক্ষণাত জবাব দিয়ে দিবেন? না চিন্তা-ফিকর করবেন? এ ব্যাপারে ইমাম আবূবকর আসকাফ (রাহ:) বলেন: যদি মাসআলা সুস্পষ্ট হয় তাহলে রাস্তায়ই জবাব দেয়া যাবে। আর যদি চিন্তা-ফিকর করতে হয়, তাহলে জবাব না দেয়াই ভাল। আল্লামা ক্বাসিম ইবনে সাল্লাম (রাহ:) এর আমল ছিল, যদি কেউ রাস্তায় প্রশ্ন করত, তাহলে তিনি কখনও জবাব দিতেন না। ফক্বীহ আবূল লাইছ (রাহ:) এ ব্যাপারে পরামর্শ দেন যে, প্রথমত তাকে বুঝানো হবে যে – রাস্তায় চলাকালীন সময়ে মাসআলা বলা যাবে না, এরপরও যদি জবাব নেয়ার জন্য একাগ্রতা পোষণ করে, তাহলে জবাব দেয়াই ভাল। ..
ফতোয়ার গুরুত্ব
ইসলামী শরীয়তে ফতোয়া মুসলমানদের ইসলামী জীবনের একটি অপরিহার্য ও অবিচ্ছেদ্য অংশ। একজন মুসলমানের জন্য তার জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আল্লাহ ও রাসূলেন নির্দেশ মেনে চলা অপরিহার্য বিধায়, জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহর হুকুম ও নবীর আদর্শ সম্বলিত কোরআনের প্রতিটি আয়াত ও রাসূলের প্রতিটি হাদীস এবং কোরআন-হাদীস স্বীকৃত ইলমে ফিকাহর প্রতিটি সিদ্ধান্তই ফতোয়া, যা শরীয়তের মূলনীতি দ্বারা সমৃদ্ধ।
প্রবিত্র কোরআনে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে সরাসরি বলে দেয়া কোন কোন সমাধানকে ফতোয়া নামে অভিহিত করা হয়েছে। প্রখ্যাত তাফসীর বিশারদগণের ধারণায় আল্লাহ পাক তাঁর প্রদত্ব সমাধানকে ফতোয়া নামে অভিহিত করে ফতোয়া শব্দটিকে মহিমান্বিত করে ফতোয়ার গুরুত্ব ও মর্যাদা মানবজাতিকে অনুধাবন করার সুযোগ দিয়েছেন।
স্বর্ণালী যুগে ফতোয়া
আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (স:) স্বয়ং ফতোয়া প্রদান করেছেন। সাহাবায়ে কেরাম (রা:) এর মধ্যে যাঁরা বিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান আলেম ছিলেন, তাঁেদরকে ফতোয়া প্রদানের জন্য নিয়োজিত করা হয়েছিল। শুধু তা-ই নয়, ইসলামী জ্ঞান ও শাস্ত্রের বিধান তথা ফতোয়া প্রদান করা প্রত্যেক জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য অপরিহার্য করে দেয়া হয়েছিল। বলা হয়েছে, জ্ঞান থাকা সত্তে¡ও যদি কেই কোন প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাব না দেয়, তার হাশরের ময়দানে তার মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে”। (আল-হাদীস)
দ্বীনী ইলমের প্রচার প্রচার-প্রসারের ক্ষেত্রে ও অজ্ঞজনদের পক্ষে জানার আগ্রহ এবং জানা-শোনাদের পক্ষে আগ্রহীদের প্রশ্নের জবাব দেয়ার যে প্রথা স্বয়ং আল্লাহর রাসূলের সময়কাল থেকে প্রচলিত, এটিই বলতে গেলে ইসলামী জীবনধারার মূল চালিকাশক্তি, ইসলামী জীবন যাপনের মূল পাথেয়। হুজুর (সা:) এর সমাধানগুলি হাদীস শরীফের বিপুল ভান্ডারে সংরক্ষিত হয়েছে। সাহাবীগণের সিদ্ধান্তগুলি “আছারে সাহাবা” নামে বিদ্যমান আছে। তাবেয়ীগণের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত উম্মতের বিজ্ঞ আলেমগণের সিদ্ধান্তসমূহ ফিক্বাহ শাস্ত্রে মূল উপাদান হয়ে আছে। মানুষের গতিশীল জীবনধারার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ইলমে ফিক্বাহ তথা ফতোয়া ফরায়েযের বিস্তৃতিও অব্যাহত থাকবে।
আল্লাহ তায়ালা শরীয়তের হুকুম-আহকাম, হালাল-হারাম, মোটকথা সর্বপ্রকারে ফতোয়া বর্ণনা করার লক্ষ্যেই হযরত আদম (আ:) থেকে শুরু করে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম রাসূল মুহাম্মদ (সা:) পর্যন্ত লক্ষাধিক নবী-রাসূল এ পৃথিবীতে প্রেরণ করেন। যাঁরা পৃথিবীর জন্মলগ্ন থেকে মানব জীবনের সর্বক্ষেত্রে মহান আল্লাহর বিধানাবলীকে প্রচার-প্রসার করে গেছেন। নবীগণ তাদের স্ব স্ব যুগের মানুষের জীবনের সমস্যাবলীর সমাধান তথা ফতোয়া দিতেন তাদের আসমানী জ্ঞানের আলোকে। এভাবেই এই পৃথিবীতে সূচনা হয় ফতোয়ার। এবং কালক্রমে ফতোয়া প্রদানের এ সুমহান দায়িত্বে সমাসীন হয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি সময়ের এমন একটি নাজুক মূহুর্তে পৃথিবীতে প্রেরিত, যখন আইয়্যামে জাহিলিয়াতের ঘোর অমানিশা চতুর্দিক আচ্ছন্ন করে নিয়েছিল। তাঁর দিক নির্দেশনা ও ফতোয়ার মাধ্যমে পৃথিবীর সবচেয়ে বর্বর জাতি খুঁজে পেয়েছে শান্তি এবং মুক্তির পথ। এর দ্বারা গড়ে উঠেছে স্বর্ণযুগের স্বর্ণ মানুষ হিসেবে। হুজুর (সা:) এর যুগের সকল সমস্যার সমাধান বা ইস্তেফতার জবাব কোরআনের মাধ্যমেই তিনি প্রদান করতেন, আবার অনেক সময় সমস্যা বা প্রশ্ন উপস্থাপিত হলে তখন কোরআনের আয়াত ও ফতোয়া হিসেবে অবতীর্ণ হতো। পবিত্র কোরআনে এর অনেক উদাহরণ রয়েছে।
যেমন:
হযরত উমর ও মুআয (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) সহ একদল সাহাবায়ে কেরাম হুজুরের দরবারে এসে ফতোয়া চাইলেন যে, মদ্যপান সম্পর্কে ফতোয়া প্রদান করুন। তখন আল্লাহ নিজেই ফতোয়া প্রদান করত নিম্নোক্ত আয়াত অবতীর্ণ করেন। ..অর্থাৎ তারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবে। বলে দাও, এগুলোর উভয়টার মধ্যে রয়েছে মহাপাপ। আর মানুষের উপকারিতাও রয়েছে। তবে এগুলোর পাপ উপকারিতা অপেক্ষা অনেক বড়। (সূরায়ে বাকারাহ, আয়াব নং ২১৯) (মা’আরিফ: ১১০)হযরত আদী ইবনে হাতিম ও যায়েদ ইবনে মুহালহাল (রা:) একদা হুজুর (সা:) এর নিকট গিয়ে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল (সা:)! মৃত জন্তু খাওয়া হারাম। এখন আমাদের জন্য বস্তু কী? এ ফতোয়া চাওয়া হলে নিম্নোক্ত আয়াত ফতোয়ারূপে অবতীর্ণ হয়। .. অর্থাৎ, হে নবী! আপনাকে তারা জিজ্ঞেস করে হালাল বস্তু কী? আপনি তাদেরকে ফতোয়া দিয়ে দিন, তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ হালাল করে দেয়া হয়েছে। (সূরায়ে মায়েদাহ আয়াত নং ৪, মা’আরিফ: ৩০৭)
মহিলাদের ঋতুস্রাব হলে ইহুদী সম্প্রদায় ঐ সব মহিলাদের সাথে উঠা-বসা থাকা-খাওয়া সর্ব প্রকারের সম্পর্ক ছিন্ন করে দিত। অপরদিকে খ্রীষ্টানরা ঐ সব মহিলাদের সাথে ঋতুস্রাব চলাকালীন সঙ্গমও করত। এমতাবস্থায় মুসলমানরা কী করতে পারে? এ নিয়ে নবীজির কাছে ফতোয়া চাওয়া হলো। তখন নিম্নোক্ত ফতোয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়। .. অর্থাৎ “আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে মহিলাদের ঋতুস্রাব সম্পর্কে। বলে দাও, কাজেই তোমরা হায়েজ বা ঋতুস্রাব অবস্থায় স্ত্রীগমণ থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়, আর যখন উত্তমরূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমণ করে তাদের কাছে যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন। (সূরায়ে বাকারাহ, আয়াত নং ২২২)
উপরোক্ত উদাহরণগুলোতে বর্ণিত ঘটনা বা প্রশ্নের জবাবে অবতীর্ণ আয়াতসমূহ ছিল – ফতোয়া। আর আল্লাহর প্রত্যাদেশ লাভ করে এ ফতোয়া প্রদান করেন মুহাম্মদ (সা:) নিজেই। অনুরূপভাবে কোরআনের এক একটি আয়াত এক একটি ফতোয়া। আল্লাহ হলেন ফতোয়াদাতা-মুফতী। আর আল্লাহর পর বড় ফতোয়াদাতা মুহাম্মদ (সা:)।
মহানবী (সা:) এর ইন্তেকালের পর ফতোয়ার মসনদে সমাসীন হলেন তাঁরই গড়া উজ্জ্বল তারকাতুল্য বাহিনী সাহাবায়ে কেরাম (রা:)। তাঁরা তাদের সততা, নিষ্ঠা, সুগভীর জ্ঞান ও যোগ্যতার ভিত্তিতে ফতোয়া দেয়ার মত মহা মর্যাদাপূর্ণ কাজটির সুমহান দায়িত্বে আত্মনিয়োগ করেন। এ কাজের জন্য প্রিয়নবী (সা:) সুনির্দিষ্ট নীতিমালার প্রতিও দিকনির্দেশনা দিয়ে যান এবং সে সব নীতিমালার প্রকৃত অনুসরণ করেই সাহাবাগণ এ মহা মর্যাদাপূর্ণ কাজটি অতীব সফলতার নাথে আঞ্জাম দিয়ে যান।
সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে যাঁরা অনেক শ্রম ও নিষ্ঠার সাথে ফতোয়ার কাজ আঞ্জাম দিয়ে যান, তাদের সংখ্যা নিয়ে কিছু মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ ৮ জন মুফতীর নাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে ৫ জন কুরাইশী এবং ৩ জন আনসারী। ইমাম সুয়ূতী (রাহ:) কর্র্তৃক তৈরীকৃত একটি তালিকার মধ্যে ২৫ জন মুফতীর নাম পাওয়া যায়। আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (রাহ:) এর মতে মুফতীদের সংখ্যা ১৩০ এর চেয়েও কিছু বেশী বলে উল্লেখ করেন।
সাহাবী মুফতীগণকে তাদের বর্ণনাকৃত মাসায়েল ও ফতোয়ার সংখ্যানুযায়ী ৩ শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। (১) অধিক ফতোয়া প্রদানকারীগণ (২) মধ্যম সংখ্যক ফতোয়া প্রদানকারীগণ (৩) তুলনামূলক ফতোয়া প্রদানকারীগণ।
অধিক ফতোয়া প্রদানকারীগণের মধ্যে ৭ জন সাহাবীর নাম উল্লেখযোগ্য। যেমন: (১) হযরত উমর (রা:), (২) হযরত আলী (রা:), (৩) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা:), (৪) আম্মাজান হযরত আয়েশা (রা:), (৫) হযরত যাইদ বিন ছাবিত (রা:), (৬) রয়ীছুল মুফাসসিরীন হযরত আব্দ্ল্লুাহ ইবনে আব্বাস (রা:), (৭) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা:)।
মধ্যম সংখ্যক ফতোয়া প্রদানকারীগণের সংখ্যা ছিল ২০ জন। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন: (১) হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা:), (২) হযরত উম্মে সালামা (রা:), (৩) হযরত আনাস (রা:), (৪) আবূ হুরাইরা (রা:),(৫) উসমান ইবনে আফ্ফান (রা:), (৭) সালমান ফারসী (রা:)।
তুলনামূলক নিতান্ত স্বল্প সংখ্যক ফতোয়া প্রদানকারীগণের সংখ্যা ১২২ জন।
সাহাবায়ে কেরামের অবর্তমানে তাদের স্থলাভিষিক্ত হন তাদেরই গড়া যোগ্য উত্তরসূরী তাবেঈনে কেরাম (রাহ:)। যেমন হযরত হাম্মাদ বিন সুলাইমান (রহ:), ইমামে আ’যম আবূ হানীফা (রহ:), হযরত আলক্বামা (রহ:), হযরত ইবরাহীম নাখয়ী (রহ:) প্রমুখ।
কিন্তু তখনও ফিক্বহের বিষয়গুলো সংকলিত হয় নি। কালক্রমে মানুষের চাহিদা ও প্রয়োজন দ্রæত গতিতে বেড়ে চলে। তারা নতুন নতুন আবিষ্কারের নেশায় মত্ত হয়। এদিকে মানুষের সরল জীবন, সরল মনন, যা সাহাবায়ে কেরামের ভূষণ ছিল, ধীরে ধীরে বিগড়ে যাচ্ছিল। চিন্তা, চেতনা, রুচি, অনুরাগ তীব্র বেগে পরিবর্তন হচ্ছিল। আবার নির্ভরযোগ্য উলামা-ফুক্বাহাগণের সংখ্যাও দিন দিন লোপ পাচ্ছিল। ফলে ফিক্বহের দুর্গম পথটিকে সঙ্কল ও বিন্যাসের মাধ্যমে সুগম করা এবং মাসআলা-মাসায়েল ও ফতোয়া প্রদানের কিছু নিয়ম-নীতি প্রণয়ন এবং মানদÐ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন তীব্রভাবে দেখা দিল। সময়ের এ অনিবার্য দাবী পূরণে প্রাজ্ঞ ও বিজ্ঞ উলামা-ফুক্বাহার এক বিশাল জামাত এগিয়ে আসেন।
আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রাহ:) ফতোয়ায়ে শামীর ৬২ নং পৃষ্ঠায় লিখেন: হযরত আবূ হানীফা (রাহ:) এর সঙ্গে তার এক হাজার শিষ্য যোগ দেন। তাদের মধ্যে ৪০ জন ছিলেন শ্রেষ্ঠ প্রধান যারা ইজতেহাদের স্তরে উন্নিত ছিলেন। উক্ত ৪০ জনের সমন্বয়ে গঠিত ফিক্বহ বোর্ডের প্রচেষ্টায় ইলমে ফিক্বহ ও মাসআলা মাসায়েল সুবিন্যস্ত হয়। মাযহাব প্রবর্তীত হয়। মাসায়েল ও ফতোয়ার মূলনীতি ও মানদÐ প্রণিত হয়। ফলে পরবর্তী ফিক্বহবিদ ও মুফতীদের জন্য ইলমে ফিক্বহ চর্চা ও ফতোয়া প্রদানের সেই মহান দায়িত্ব পালন খুবই সহজ হয়। সাহাবা, তাবেঈন, তবে’ তাবেঈন থেকে নিয়ে আইম্মায়ে মুজতাহিদীনের সেই পথ ধরে ফতোয়া প্রদানের এ মহান দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়ে আসছেন উলামায়ে হক্কানী ও মুফতীয়ানে কেরাম। এবং এ মহান আদর্শটি সমুন্নত ও উজ্জীবিত রাখতে অবিরাম চেষ্টা চালিয়েছেন তাঁরা। এরই ফলশ্রুতিতে অন্তত ধর্মীয় বিধি-নিষেধ বা মাসআলা মাসায়েলের ক্ষেত্রে নতুন পুরাতন সমস্যাবলীর সমাধানকল্পে ও মুসলিম সমাজকে সম্ভাব্য মতানৈক্যের কুফল থেকে রক্ষার জন্যে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আসছে ফতোয়া বিভাগ বা দারুল ইফতা। এখনো পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে এ ধরণের দারুল ইফতা বিদ্যমান। আর এভাবে সবত্রে দারুল ইফতা থাকার অতি প্রয়োজন। কারণ এ ফতোয়া ছাড়া ইসলামের বিধি-বিধান প্রণয়ন করা কষ্মিনকালেও সম্ভব নয়। ইসলামের প্রথম থেকে এর প্রচলন চলে আসছে, যা আজও আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। আর থাকবে না কী করে? কারণ এটা ইসলাম তথা সমস্ত বিশ্বের মুসলিম জাতির একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেভাবে একজন মানুষ তার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মুখাপেক্ষী। এগুলো ছাড়া সে অচল। ঠিক তেমনিভাবে ফতোয়া ছাড়া মুসলমানী জীবন অচল। সবাই এটার মুখাপেক্ষী। এটাই সঠিক পথের দিশারী। এ ফতোয়াই একমাত্র মানুষকে প্রবৃত্তিক খারাপ কাজসমূহের দিকে ধাবিত হওয়া থেকে বিরত রাখে। এবং সৎ কাজের সন্ধান দেয়। যেমন, এর উদাহরণ হিসেবে বাদশাহ আলমগীরের ঘটনাটি স্মরণ করা যেতে পারে।
কথিত আছে যে, বাদশাহ আলমগীর রাজস্ব ভান্ডারের অর্ধেক অর্থ ব্যয় করে দিতেন ফতোয়ার কাজে। এসব দেখে তাঁর মা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, ফতোয়ার পিছনে তুমি কেন এত টাকা-কড়ি ব্যয় কর? তিনি উত্তর না দিয়ে তাঁর এক কর্মচারীকে বললেন, তুমি একটি পাঠাবাচ্চা এবং ঐ বাচ্চার মা (ছাগী)কে নিয়ে এসো। যেই কথা সেই কাজ। ছাগী ও তার প্রাপ্তবয়স্ক বাচ্চাকে নিয়ে আসা হলো। অতপর মা-বাচ্চা, পাঠা-পাঠি দুটোকেই বাদশাহ আলমগীরের মায়ের সামনে ছেড়ে দেওয়া হল। তখন দেখা গেল, পাঠা তার জন্মদাত্রী মায়ের পিঠে উঠতে শুরু করেছে (যৌন তৃপ্তি মেটানোর জন্য)। মা এবং সন্তানের মধ্যে কোন প্রকার ভেদাভেদ লক্ষণীয় হল না। এবার বাদশা ব্যবহারিকভাবে দেখিয়ে তাঁর মাকে বললেন, যদি ফতোয়ার কার্য না থাকে তাহলে মানুষের চরিত্র এমন হয়ে যাবে- যা আমরা দুই ছাগলের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি।
আজ আমাদের দেশে ফতোয়ার শক্তি হ্রাস পাওয়ায় এবং ফতোয়ার বাস্তব প্রয়োগ না থাকায় আমরা খবর পাচ্ছি মেয়ের পেটে পিতার সন্তান, বোনের পেটে ভাইয়ের সন্তান, নানীর পেটে নাতীর সন্তান, মায়ের পেটে ছেলের সন্তানের কথা। সুতরাং ফতোয়া কেন? তার কী গুরুত্ব? কী প্রয়োজন? এ সকল প্রশ্নের উত্তরে বলতে হয়, মানুষের প্রবৃত্তিকে সঠিক পথে এবং মানুষের জীবনকে পঙ্কিলতামুক্ত করে পরিচালনা করার জন্যই হলো ফতোয়া। যাতে করে প্রবৃত্তি মানুষকে পশুত্বের পর্যায়ে নামিয়ে না ছাড়ে। তাই প্রাত্যহিক জীবনে ফতোয়া বা হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েস, তথা ইসলামের বিস্তর নীতিমালার গুরুত্ব মুসলমানের নিকট অপরিসীম। আরো বলতে গেলে এর গুরুত্ব শুধু মুসলমানদের বা মুসলিম রাষ্ট্রের মধ্যে সীমিত নয়, বরং অনেক অমুসলিম দেশেও ফতোয়ার গুরুত্ব রয়েছে। যেমন, জার্মানির একটি ঘটনা থেকে এ-র সুস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।
ঘটনাটি হল: জার্মানিতে মুসলিম ছাত্রীদের স্কুলে যেতে মাথায় ওড়না ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিল সেখানের একটি স্কুল কর্তৃপক্ষ। তখন মুসলিম ছাত্রীদের অভিভাবকগণ সে দেশের আদালতের শরণাপন্ন হলে আদালতের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেয়া হয়, ওড়না ব্যবহার মুসলমানদের ধর্মীয় বিধান কি-না? ফতোয়ার জন্য পাঠানো হয় মদীনা ইউনিভার্সিটিতে। সেখান থেকে ফতোয়া প্রদান করা হয় যে, ‘‘ইসলাম ধর্মের অনুসারী মহিলাদের জন্য মাথায় ওড়নাসহ শালীন পোশাক পরিধান করা ধর্মীয় কর্তব্য তথা ফরজ।’’ উক্ত ফতোয়া জার্মানির আদালতে পাঠানো হলে আদালত রায় দেয় যে, মুসলিম ছাত্রীদের ওড়না পরা তাদের ধর্মীয় অধিকার। সুতরাং স্কুল ছাত্রীদেরকে মাথায় ওড়না ব্যবহার করতে বাধা দেয়া যাবে না।
কিন্তু দু:খজনক হলেও সত্য যে, ইসলামী অন্যান্য নীতির ন্যায় ধীরে ধীরে এ মহানাদর্শটিও মুসলিম সমাজ হতে লোপ পেতে থাকে। ফলে মুসলিম উম্মাহর মাঝে বিভিন্ন বিষয়ে তীব্র মকানৈক্যের সৃষ্টি হচ্ছে। যার বিষাক্ত ছোবলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে মুসলিম উম্মাহ। টুকরো টুকরো হয়ে গেছে তাদের ঐক্যের প্লাটফর্ম। এমতাবস্থায়ও সেই মহানাদর্শকে ধরে রেখেছেন হাতেগুণা মুষ্টিময় হক্কানী ওলামা ও মুফতীয়ানে কেরামগণ। ফতোয়া ও তার গুরুত্বকে বুঝা যেহেতু শুধু কয়েকজন মুফতী ও আলেমের দায়িত্ব নয়, বরং সমস্ত মুসলিম জাতির দায়িত্ব। তাই ফতোয়া কী ও কেন? এ সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে সাথে সাথে আমল করা প্রতিটি মুসলমানের জন্য অপরিহার্য।
ফতোয়ার অপব্যবহার বনাম ফতোয়াবাজী
ফতোয়া ইসলামী আইনের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ দায়িত্ব গ্রহণ করা সর্বলোকের কাজ নয়। এটা একমাত্র ঐ ব্যক্তির কাজ যার মধ্যে পূর্বোল্লিখিত শর্তাবলী বিদ্যমান। যে কোন কেউ ফতোয়া প্রদানের অধিকার রাখে না। তা সত্তে¡ও যদি কোন অযোগ্য ব্যক্তি ফতোয়া প্রদান করে, তাহলে তা হবে ফতোয়ার অপব্যবহার। সাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈন ফতোয়া প্রদানে খুবই সর্তকতা অবলম্বন করতেন।
ইমাম নববী (রাহ:) সাহাবায়ে কেরাম সম্পর্কে বর্ণন করেন, প্রত্যেক সাহাবী অতি সর্তকতামূলক মনোভাবের কারণে কোন একটি হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এটা পছন্দ করতেন যে, ‘যদি অন্য কোন ভাই হাদীসটি বর্ণনা করতেন এবং আমাকে বর্ণনা করতে না হতো।’ কোন বিষয়ে ফতোয়া চাওয়া হলে বলতেন, ‘আহ! আমার পরিবর্তে অন্য কেই যদি ফতোয়াটি প্রদান করত!’
ইমাম মালিক (রাহ:) বলেন, ৭০ জন নির্ভরযোগ্য আলেম আমাকে ফতোয়া দেয়ার যোগ্যতার স্বীকৃতি প্রদান না করা পর্যন্ত আমি কোন ফতোয়া প্রদান করি নি। অন্তরে আল্লাহ এবং পরকালের ভয়পোষণকারী কোন ব্যক্তি ফতোয়া প্রদানে বেপরোয়া হতে পারে না। এক হাদীসে এসেছে, ফতোয়া দেয়ার ক্ষেত্রে যে যত বেশী সাহসী, সে জাহান্নামের পথে তত বেশী সাহসী। তাই ফতোয়ার যথার্থ প্রয়োগ যেমন মহা কল্যাণকর এবং এর প্রয়োজন অপরিহার্য, তেমনিভাবে অপপ্রয়োগও ডেকে আনে সমূহ অ-কল্যান, চরম বিপর্যয়। কেননা ফতোয়া শব্দটি অতি পবিত্র। স্বয়ং আল্লাহ তার পবিত্র কালামে এ শব্দকে বিভিন্ন স্থানে ব্যবহার করেছেন, যেমন পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বুঝা যায় যে, ইসলাম ধর্মে আল্লাহর পবিত্র বিধান ও তার ব্যাখ্যাকে ফতোয়া বলা হয়। আর আল্লাহর বিধানের যারা অপব্যবহার করে ও অবিশ্বাসী হয়, এদেরকেই বলা হয় খোদাদ্রোহী বা ‘কাফের’। কারণ আল্লাহর বিধান যারা অবিশ্বাস করে, তারা স্বয়ং আল্লাহকেই অবিশ্বাস করে। কেননা মানুষের জন্য যা কিছু কল্যাণকর সেগুলিকেই আল্লাহ হালাল এবং যা অকল্যাণকর সেগুলিকেই হারাম বলে ফতোয়া দিয়েছেন।
সুতরাং ইসলামে ঘোষিত কোন হালালকে হারাম, বা হারামকে হালাল হিসেবে বিশ্বাস করার নামই হচ্ছে আল্লাহর বিধানকে অমঙ্গলজনক মনে করা। আর এরই নাম কুফর বা খোদাদ্রোহীতা। এক কথায় যারা আল্লাহর ফতোয়া মানে না তারা কাফের। কাফের দুই প্রকার: এক প্রকারের কাফের পরিষ্কারভাবেই আল্লাহর প্রতি অমান্য, তথা ইসলাম ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসের ঘোষণা দিয়ে থাকে। দ্বিতীয় প্রকারের কাফের ইসলামের ছদ্মাবরণে ইসলামী অনুশাসনের প্রতি বৈরী মনোভাব পোষণ করে থাকে। ইসলামী পরিভাষায় উক্ত দ্বিতীয় প্রকারের কাফেরকেই মুনাফিক নামে আখ্যায়িত করা হয়। আর এরা প্রকাশ্য কাফেরদের চেয়ে আরো জঘন্য।
আসুন এবার আমরা জেনে নেই “ফতোয়াবাজ” শব্দটির বিশ্লেষণ। যার থেকে বুঝতে পারবো যে, কারা ফতোয়াবজ? এবং কিসের নাম ফতোয়ার অপব্যবহার? এবং কী গুরুত্ব ফতোয়ার?
“ফতোয়াবাজী” বা “ফতোয়াবাজ” এ ধরণের কোন শব্দ ইসলাম ধর্মে খোঁজে পাওয়া যায় না। ফতোয়া এবং ফতোয়াবাজী ভিন্ন ভিন্ন অর্থবোধক দু‘টি শব্দ। শব্দ দু‘টির মর্মদ্বয়ে রয়েছে আকাশ পাতাল ব্যবধান। কিন্তু আধুনিককালের প্রগতিবাদীর নামে কিছু প্রাচীনবাদী, পাণ্ডিত্যের নামে মুর্খতার পরিচায়ক – হয়ত জেনে-শুনে সত্য গোপনের কুট কৌশল হিসেবে, আর না হয় চরম অজ্ঞতার কারণে – শব্দ দু‘টিকে ঢালাওভাবে একই অর্থে ব্যবহার করার বিভ্রান্তিকর অপপ্রচারে লিপ্ত হয়েছে। এদের মস্তিষ্ক মূলত আন্তর্জাতিক আগ্রাসী শক্তি ইয়াহুদ, নাসারা এবং নাস্তিক্যবাদীদের দ্বার ধোলাইকৃত। তদুপরী সবচেয়ে মারাত্মক বিভ্রান্তিকর ব্যাপার হলো এদের অধিকাংশই মুসলমানরূপে পরিচিত এবং মুসলমান মাতা-পিতার সন্তান। যদি এরা নিজেদের মুসলিম পরিচিতিটা প্রকাশ্যে মুছে ফেলত, তবে এদের অপপ্রচারণা অন্যের জন্য ততটুকু বিভ্রান্তিকর হয়ে দাঁড়াত না। ফতোয়াবাজী শব্দ ব্যবহারের দ্বারা এদের মূল উদ্দেশ্য হলো, শব্দটিকে হাস্যের বস্তুতে পরিণত করা। এ শব্দের প্রতি জনমনে বিরাগ, অপ্রীতি, অবজ্ঞা ও ঘৃণা সৃষ্টি করা। ফতোয়া প্রদানকারী সম্মানিত আলেম ওলামা ও মুফতীদের প্রতি সাধারণ জনতাকের বীতশ্রদ্ধ করে তোলা।
“বাজী” শব্দটি মূলত ফার্সী। এর অর্থ খেলা করা। সুতরাং ফতোয়াবাজীর অর্থ দাঁড়ায় ফতোয় নিয়ে খেলা করা। যা ইসলামের সাথে চরম ঔদ্ধত্য প্রদর্শন, ইসলামী পরিভাষা নিয়ে জঘন্যতম ব্যঙ্গ-বিদ্রোপ করা। যার অনিবার্য পরিণাম ইসলাম থেকে বিচ্যুত হয়ে যাওয়া। শরীয়তের বিধি-বিধান না মানা এক কথা, আর কোন বিধি-বিধানকে নিয়ে ব্যঙ্গ করা ভিন্ন কথা। আমল না করলে ঈমান যায় না, গুনাহ হয়। কিন্তু ব্যঙ্গ বিদ্রোপ করলে ঈমান চলে যায়। তাই ইসলামী পরিভাষা নিয়ে ব্যঙ্গ করা জঘন্যতম অপরাধ। ফতোয়া ইসলামী আইনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এই ঐতিহ্যবাহী পরিভাষাটিকে ব্যঙ্গ করে এর সাথে বাজী শব্দ যুক্ত করে একে নিয়ে ঠাট্টা বিদ্রোপ করার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছে তথাকথিত প্রগতিবাদীরা। অথচ এ বাজী শব্দটি ব্যবহার হয় সমাজের সবচেয়ে নোংরা বিষয়ে, যেমন: চালবাজী, ধোকাবাজী, চাঁদাবাজী ইত্যাদি। সুতরাং বাজী শব্দ যোগ করে ফতোয়ার প্রতি ঘৃণা ছড়িয়ে দেয়ার তৎপরতা সত্যিই অত্যন্ত দুঃখজনক। এরা মানবাধিকারের ধোঁয়া তুলে, মানবদরদী সেঁজে, আলেম ওলামাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। সুতরাং এটাও ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার মধ্যে শামীল।
১৮০৩ সালে ইংরেজ শাসনের নাগপাশ থেকে উপমহাদেশকে মুক্ত করার লক্ষ্যে যে পবিত্র জিনিসটি মুসলমানদের অন্তরে প্রেরণার উৎস হিসেবে বদ্ধমূল হয়েছিল, সেটি ছিল একটি ফতোয়া। ফতোয়াটি জারি করেছিলেন উপমহাদেশের কৃতি সন্তান হযরত শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিসে দেহলভী (রাহ.)। ফতোয়ার বিষয় বস্তু ছিল, “ভারত দারুল হারব” অর্থাৎ অমুসলিম শাসিত মুসলিম নির্যাতিত দেশ। এখানে ইংরেজ উৎখাতের জন্য জিহাদ করা ফরয। ঠিক সে সময়ে ইংরেজ বেনিয়াদের চক্রান্তের শিকার হয়ে পাঞ্জাবের কুখ্যাত মিথ্যা নবীর দাবীদার মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, অর্থের লোভে মুসলিম মিল্লাতে ফাটল ধরানোর জন্য এক জঘন্যতম ফতোয়া দিয়ে বলে, “ভারত দারুল হরব নয়”। এখানে জিহাদ করা হারাম। এই ফতোয়াকে অবশ্যই ফতোয়াবাজী বা ফতোয়ার অপপ্রয়োগ বলা যেতে পারে। ইসলামের চার মূলনীতি ব্যতিরেকে মনগড়া কোন সমস্যার সমাধান দিলে এটাই ফতোয়ার অপব্যবহার। ফতোয়া সম্পর্কে এক উর্দুভাষী বুজুর্গ বলেন, … অর্থাৎ এ পৃথিবীতে সর্বকঠিন কাজ হলো ফতোয়া দেয়া”। সুতরাং কোরআনের দু‘ একটি আয়াত বা সূরা পড়ে, বাংলা তাফসীর ও বাংলা বুখারী শরীফ পড়ে ফতোয়া দেয়া কারো জন্য জায়েয নয়। এরপরও যদি কেউ ফতোয়া দেয়, তাহলে সে হবে ফতোয়াবাজ। এবং তার ফতোয়া প্রদান হবে ফতোয়ার অপব্যবহার। যেহেতু একজন মুফতীকে বিভিন্ন শর্তাবলীর অধিকারী হতে হয়, তাই শর্ত ছাড়া ফতোয়া প্রদানকারী হবে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে ডাক্তারী পড়া ছাড়াই প্রেসক্রিপশন লিখে। সেই ব্যক্তি যেমন ধোকাবাজ, ফতোয়ার জ্ঞান ছাড়া ফতোয়া প্রদানকারীও ধোকাবাজ, ফতোয়াবাজ।
আমাদের বাংলাদেশেও ফতোয়াবাজদের একটি গ্রোপ বিদ্যমান। যারা ইহুদী, খৃষ্টানদের পৃষ্টপোষকতা প্রাপ্ত কিছু এনজিও এবং তাদের পোষ্য একটি শ্রেণী। যারা সেবার নামে দেশে কাজ করছে। বিশেষত “আশা”, “ব্রাক” ইত্যাদি যে সেবার নামে শোষণ এবং ইসলামের বিরুদ্ধে জঘন্য প্রচারণা চালাচ্ছে। এ সকল ধর্মদ্রোহী শোষণবাদী এনজিওরা ফতোয়ার বিরুদ্ধে। আমাদের জানামত তাদের আসল মতলব হল, যেহেতু শরীয়ত নিয়ন্ত্রিত জীবন ব্যবস্থার মধ্যে মনগড়া চলার অবকাশ নেই। মুসলিম সমাজ ফতোয়া দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিধায় এখনো সমাজে শালীনতা বজায় আছে। এখনো মুসলিম দেশগুলোতে পাশ্চাত্যের মত অবাধ মিলনের প্রবাহ নেই। সুযোগ নেই পশুত্ব জিন্দেগীর। আজ পাশ্চাত্য জগতে গোটা মানব সমাজকেই যৌন কর্মের আড্ডা তৈরীর কর্ম কৌশল উদ্ভাবনে ব্যস্ত। মোটকথা, ফ্রী সেক্স চর্চার প্রধান প্রতিবন্ধকই হলো ফতোয়া। এ জন্যই বর্তমানে বিশ্বময় ফতোয়া বিরুধী চিৎকার ও হুংকার। তাদের লক্ষ্য শুধু ফতোয়া নয়, লক্ষ্য হল ইসলামের উৎখাত। তাদের ভাষায়, “যতদিন বাংলাদেশে মৌলবাদের বিচরণ থাকবে, শান্তি ফিরে আসবে না”। আর আমরা বলি, “যতদিন বিশ্বের মানচিত্রে বাংলাদেশ থাকবে, ততদিন এ দেশে মৌলবাদও থাকবে। বরং এ দেশ অতিসত্ত¡র শাসন করবে মৌলবাদীরা। মৌলবাদীরাই হবে দেশের কর্ণধার এবং ফতোয়াই হবে দেশের চালি-চালিকা শক্তি।
এছাড়া বিগত ২০০১ সালে বাংলাদেশের বর্তমান ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদী আওয়ামী সরকারের সামপ্রতিক শাসনামলে সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ফতোয়াকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল। তাদের এ নিষেধাজ্ঞা জারি করা মানে শুধু ফতোয়াই বন্দ করা নয়, বরং ইসলামকে সমূলে ধ্বংস করা। কিন্তু তা বাস্তবায়ন করা কষ্মিন কালেও সম্ভব হবে না। ইনশাআল্লাহ।
উল্লেখিত ফতোয়াবাজদের ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা জরুরী। কারণ এত মুসলিম সমাজ ক্ষতিগ্রস্থ হবে। কোন ভাবেই এগুলো ইসলাম সম্মত কাজ নয়। আর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা বিশেষ কারো দায়িত্ব নয়, বরং সমাজের সকল মহলের।
আলোচনার শেষ প্রান্তে সতর্কতার জন্য কিছু ফতোয়াবাজদের নাম উল্লেখযোগ্য।
ভারত বর্ষে ফতোয়াবাজদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো: মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, সালমান রুশদী গং। আর বাংলদেশে প্রসিদ্ধ হলো: ড. আহমদ শরীফ, তাসলীমা নাসরিন, কবি শামছুর রাহমান, অধ্যাপক কবীর চৈাধুরী, ড. হুমায়ূন আজাদ, শাহরিয়ার কবীর, কবি সুফিয়া কামাল গং। এরা শুধু ফতোয়াবাজই নয় বরং চিহ্নিত মুর্তাদও বটে। যতদিন এদেশে এদের বিচরণ থাকবে, ততদিন শান্তি ফিরে আসবে না। বর্তমানে আমাদের দেশে কিছু নিউ বুদ্ধিজীবি ভাতিজা-ভাতিজী, ভাগিনা-ভাগিনী বিদ্যমান আছেন। যারা কবি সুফিয়া কামাল (মৃত: ১৯৯৯ ইং) কে খালাম্মা বলে ডাকতেন। ঐ কবি সুফিয়া রেখে গেছে তার অনুসারীদেরকে এ ধরায়। যেমন: আওয়ামী সভানেত্রী শেখ হাসিনা, জাফর ইকবাল, আবু কায়সার, মুস্তফা নূরুল ইসলাম, আতাউস সামাদ, মুনতাসীর মামুন, আহমদ ছফা, শামছুজ্জামান খান, মমতাজ উদ্দীন আহমেদ, আবেদ খান, ফরিদা আক্তার, মালেকা বেগম গং। এরাও মুর্তাদের তালিকায় অন্তর্ভূক্ত। এদের থেকেই আমাদের সজাগ থাকতে হবে। এরা বাঘ-ভালুক না হলেও শিয়াল-কুকুর তো নিশ্চই। তাই আল্লাহ পাক রাব্বুল আলামীন যেন আমাদেরকে তথা ইসলামকে বাঘ-ভালুক ও শিয়াল-কুকুরের থাবা ও হামলা থেকে হেফাজত করেন। আমীন।
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি:
১. আল কোরআনুল করীম
২. তাফসীরে মা’আরিফুল কোরআন: মুফতী শফী সাহেব (রাহ.)
৩. আল মিছবাহ ফী রাসমিল মুফতী ওয়া মানাহিজিল ইফতা: ১ম খন্ড, ২য় খন্ড, তাকমিলাহ
মুফতী মুহাম্মদ কামাল উদ্দীন আহমদ আর রাশিদী
৪. আপ ফাতওয়া কেইছে দেঁ: মাওলানা মুফতী সাঈদ আহমদ পালনপূরী
৫. ফাতওয়া নাওয়ীসী কে রাহনুমা ও উসূল: মুফতী মুহাম্মদ সালমান মনসূরপূরী
৬. মাসিক মঈনুল ইসলাম, ১৪১৪ হিজরী, জিলহজ্জ
৭. বুদ্ধিজীবী, মৌলবাদী ও ফতোয়াবজী: আশরাফ আলী নিজামপুরী
৮. আদালতের কাঠগড়ায় ফতোয়া, বিবাহ, তালাক: তৌহিদুর রহমান